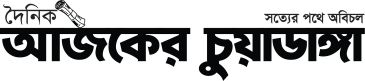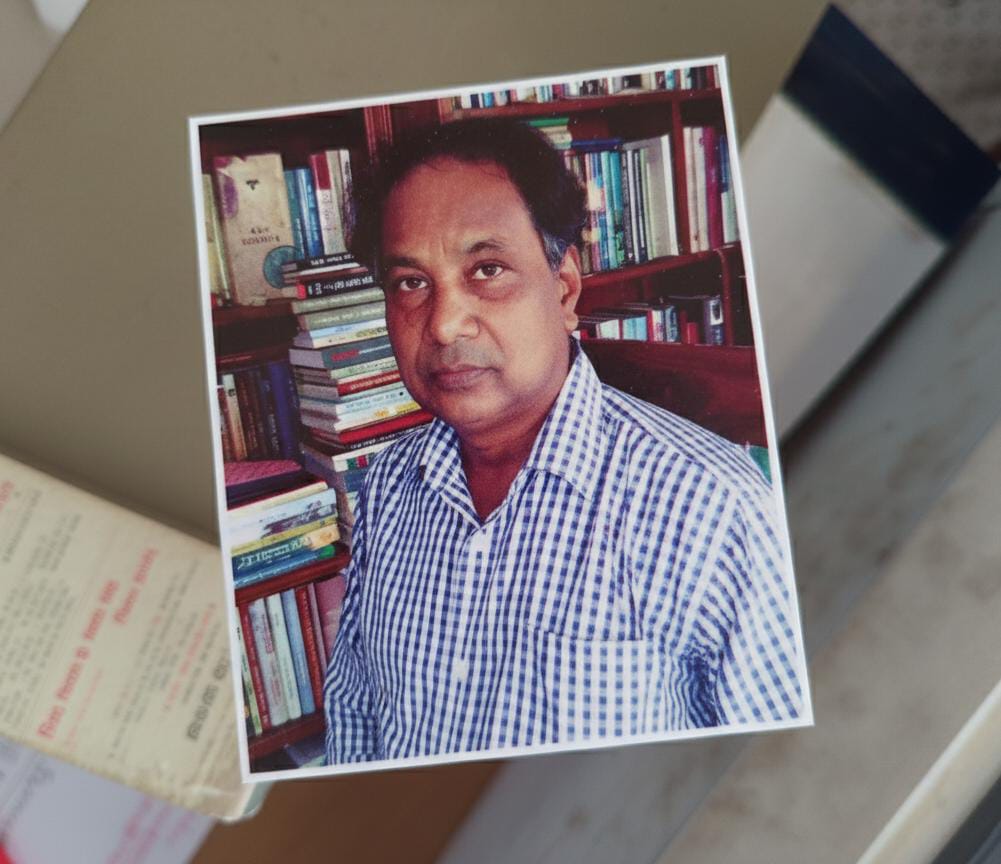ইয়েটসের সাথে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দু’বছর আগে। তখন চলছিল ইউরোপে সংস্কৃতির সংকটকাল। ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ও মানবতাবাদী সভ্যতা তখন ধ্বংসের দিকে দ্রুত ধাবমান। এই সভ্যতার নিচের তলায় ছিল কুৎসিত ও স্বার্থপর রূপ। পুঁজিবাদের দ্রুত বিকাশ, মুনাফা অর্জনের লোভ মানুষকে পরিণত করে কুটিল মানুষে। এই সময় সরল ও অপেক্ষাকৃত গভীর সংস্কৃতির মর্মস্পর্শী বাণী নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইউরোপ তা সানন্দে গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথের সাথে ইয়েটসের পরিচয়ের একটি সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পটভূমি আছে। একজন আইরিশ, অন্যজন ভারতীয়। ইউরোপের যুক্তিবাদ, বস্তুবাদ, প্রত্যক্ষবাদ আত্মাকে অস্বীকার করে সহজ উপলব্ধিকে সংশয়াক্রান্ত করে তোলে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে নিদারুণ শূন্যতার জন্ম দেয়। ইয়েটসের ভাষায়, এক বাক্স খেলনায় পরিণত হয়। ইয়েটস ভারতীয় দর্শন, চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতার সাথে পরিচিতি লাভ করে মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের দৌত্যে। সুদর্শন এই ব্রাহ্মণ যুবক ভারতীয় পৌরাণিক মিথ ব্যাখ্যা করে সমকালে আইরিশ সমাজের কাছে জ্ঞান, উপলব্ধি ও কল্পনার নতুন দিগন্ত খুলে দেন।
ভারতীয় ধ্রুপদী দর্শনের এই ব্যাখ্যাকার ইয়েটসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের বাণী তাঁর স্মৃতিতে এবং তাঁর সাহিত্য রচনায় জীবনব্যাপী অনুরণন তোলে। আসলে ইয়েটস মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের নিকট থেকে কী লাভ করেন? ইয়েটস তাঁর নিকট থেকে এমন এক দর্শন লাভ করেন যা যুক্তির অনুগামী এবং একই সঙ্গে নিঃসীম। এই দর্শনের মূল প্রত্যয় সবকিছুর উৎসমূল আত্মা। ইয়েটস জীবনের প্রথমদিকে দার্শনিক কান্টের তিনটি শব্দের উপর তাঁর সাহিত্য দাঁড় করাতে চান মুক্তি, ঈশ্বর ও অবিনশ্বরতা। কিন্তু বেকন, নিউটন ও লকের প্রভাবে এই তিনটি প্রত্যয় এক সময় ফিকে হয়ে যায়। ইয়েটসের ধারণারও পরিবর্তন ঘটে। তবে ইয়েটস শেষ জীবনে আধ্যাত্মিকতাকে একেবারে পরিহার করতে পারেননি। এখানেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মিতালি। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ায় যা শতভাগ টিকে না, তাতেও তাঁর বিশ্বাস ছিল। ইয়েটস আধুনিক মানুষ হিসাবে এমন ধর্ম চান যা ব্যক্তির সত্তাকে পরিতৃপ্ত করে, ভেতরের জগতের সাথে বাইরের জগতের আত্মিক সংহতি দান করে। ইয়েটস এও বিশ্বাস করেন অসীম বিস্তৃত দর্শনের গভীর চিন্ময়তা (চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানময় জগত)। ইয়েটস দাবি করেন যে, আমাদের সত্তার বা প্রকৃতির একটি কালাতীত স্থানাতীত দিক আছে যা হয়তো যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। তবুও আমরা যেন কল্পনায় অনেক দূর যেতে চাই। ইয়েটস মনে করেন তার জন্যও প্রয়োজন স্পন্দিত অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দার্শনিক চিন্তায় যে পাঠ ইয়েটসকে দেন, তা ইয়েটসের বিশ্বাসের সাথে অনেকটা মিলে যায়। তাঁর দর্শন-লালিত সংস্কৃতির পরম আশ্চর্য প্রকাশ তিনি রবীন্দ্রকাব্যে দেখতে পান। গীতাঞ্জলির মধ্যে বাংলাদেশের রোদভরা নিবিড় নীল আকাশের নিচে যে প্রকৃতি ইয়েটস দেখতে পান, তা ইয়েটসকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। ইয়েটসের কাছে রবীন্দ্রনাথের আবেদন ছিল মূলত সম্পৃক্ত সংস্কৃতির আবেদন, যেখানে কিষাণ ও অভিজাত শ্রেণির যোগ ছিল। সেখানে মানুষ দেহ ও আত্মাকে আলাদা করে দেখেনি।
ইয়েটস গীতাঞ্জলির ভূমিকায় বলেন: “ভারতীয় সভ্যতার মতো রবীন্দ্রনাথও আত্মাকে আবিষ্কার করেন। জীবনব্যাপী আমি যে-জগতের স্বপ্ন দেখেছি, গীতাঞ্জলি যেন আমার সেই জগতের সন্ধান দেয়। এগুলো পরম সংস্কৃতির কীর্তি। এগুলো মাটির গন্ধ থেকে বেরিয়ে এক নতুন জগত সৃষ্টি করে।” রবীন্দ্রনাথের দেহ ও আত্মার অনায়াস মিলন ইয়েটসকে বেশি আকৃষ্ট করে। ইয়েটস বলেন, পবিত্রতার অনুভূতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ধর্মচর্চার অনুভূতি নয় বা আত্মনিগ্রহের অনুভূতি নয়। এ অনুভূতি ধুলো আর সূর্যালোকের ছবি আঁকে। আধুনিক কালে খণ্ডিত সমাজ, কালচেতনা এবং খণ্ডিত জ্ঞানের জন্য ইয়েটস ক্লিষ্ট বোধ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে জীবন ছিল চিরন্তন মানবীয় ঐক্যের মহা আহ্বান, যা ইয়েটসকে মুগ্ধ করে। ইয়েটস দ্বন্দ্বকে চিন্তার অভিজ্ঞতার, ব্যক্তি ও বিশ্বের সম্পর্কের মূলনীতি বলে মনে করেন। আর রবীন্দ্রনাথের ঐক্যবোধ অনায়াসলব্ধ, যা ছিল জীবনের মূলনীতি। যে কারণে রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্ববোধ তীব্র হয়নি। ইয়েটস একবার বলেছিলেন: “প্রাচ্যের কাছে সব কিছুর সমাধান আছে, তাই সে ট্রাজেডি কাকে বলে জানে না।” তবে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মবোধে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আসে। ইতিহাসের নানা অভিঘাতে তাঁর বিক্ষুব্ধ মনে অনেক প্রশ্ন জাগে। সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য তাঁর চিন্তাকে তিনি ঐতিহ্যসীমার বাইরে নিয়ে যান। আবার ঐতিহ্যিক কাঠামো থেকে ভাব বা রূপকল্প নিয়ে তিনি চিন্তাকে দৃঢ়তা দেন। মানুষের নিঃসঙ্গ দুঃখ, প্রাণলোকের প্রতিকারহীন যন্ত্রণা, ইতিহাসের নির্মম অন্যায়, অশুভ ঐতিহ্যলব্ধ রহস্যময় বিধাতার বিশ্বাস তাকে বিচলিত করে। পরিণামে তিনি এমন এক বিধাতার ধারণায় উপনীত হন, যিনি মঙ্গলময় নন, মানবোত্তীর্ণ; বরং মানুষের অধিগম্য এক প্রকাশমান মানব-ভগবান, যাকে মানুষের ভাগ্যের জন্য দায়ী করা যায়, মানুষের পূর্ণতায় যার পূর্ণতা। তবে রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটসের ঈশ্বরবোধ এক ধরনের ছিল না। একজন পরম সুন্দরকে অন্তর্লোকে ও বহির্লোকে প্রতিক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন—রূপের বর্ণচ্ছটায় তার প্রকাশ দেখতে পান। আরেকজন কাব্যের ধ্বনি ও মিলের প্রয়োজনে ঈশ্বরের মহিমাকে বিশ্বকল্পনায় পূর্ণতা দেন। অহংবাদী ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো মন্ময় সম্পর্ক ঈশ্বরের সাথে স্থাপন করেননি। এ কারণে তাঁর কবিতায় ঈশ্বর মন্ময় অনুভূতির অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ছিল সূর্যকর কিংবা বাতাসের মতো তাকে তিনি এড়াতে পারেননি। তবে তাঁর চিন্তায় নানা বেশে ঈশ্বর ধরা দেন।
রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে, তাঁর মনের দৃঢ়তা, আবেগের সংযম, ভাষার মিতাচার, ব্যঞ্জনার তীক্ষ্ণতা ও জটিলতা তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্য ইয়েটসের পরিণত রচনার সাথে তুলনীয়। এই দুই কবির প্রকৃতি ও মানসিক অবয়ব সম্পূর্ণ ভিন্ন। বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ইয়েটস থেকে কিছু গ্রহণ করেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তায় এক সময় ইয়েটস মুগ্ধ হন। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ইয়েটসও রবীন্দ্রনাথের নিকট থেকে তেমন কিছু গ্রহণ করেননি। তাই তাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনায় অকিঞ্চিতকর। তবে ইয়েটস রোডেনস্টাইনের নিকট স্বীকার করেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শিল্পে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন—যা ছিল অচিন্তনীয়। তবে রবীন্দ্রনাথও ইয়েটসের সাংস্কৃতিক অভিপ্সা ও আধ্যাত্মিক প্রত্যয়কে স্পষ্ট ও শক্তিশালী করেন। আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে ভারতীয়দের সাথে আইরিশদের পরিচিতির সার্থকতা আছে। জীবনের মধ্যে সত্যকে অনুভব করে বস্তুর অন্তরে আত্মাকে দেখেন। তিনি বলেন, বস্তু ও আত্মার কোনো বিচ্ছেদ নেই।
ইয়েটস বলেন, প্রতীক ও প্রতীকাতীত শেষ পর্যন্ত এক। প্রাচ্যের আকর্ষণীয় দিক হলো তার সরল স্বাভাবিক ঐতিহ্যবিন্যস্ত জীবন। তার মন্দের দিক হলো সুমিত আকার ও দৈহিক অস্তিত্বের প্রতি অবহেলা, নিরবয়বতা ও অস্পষ্টতার প্রতি ঝোঁক, স্বনিগ্রহ ও সহজ আত্মসমর্পণ প্রবৃত্তি। প্রাচ্যতের বৈশিষ্ট্য তার দেহী জীবন, বস্তুর প্রতি আনুগত্য, কল্পনার আবয়ব স্ফূর্তি এবং শত্রুভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি; এবং কালকে ইতিহাসের পটভূমিতে মূর্ত করার আগ্রহ। এই গুণগুলো ভৌগোলিক হলেও কাল নির্বিশেষে যে কোনো দেশে দেখা যেতে পারে। প্রাচ্যের সমস্ত চিত্তাকর্ষক গুণ ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখতে পান। ১৯৩১ সালে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: “আপনার কবিতা আমাকে উদ্দীপ্ত ও মুগ্ধ করে। আপনার কবিতা যখন প্রথম পড়ি, আমি দারুণ উদ্দীপনা অনুভব করি। আমার মনে হয়েছিল, এ যেন মাঠ আর নদী থেকে বেরিয়ে এসেছে তাদের অপরিবর্তনীয় সুষমা নিয়ে।” তবে ইয়েটস মনে করেন, ইউরোপের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি সম্ভব হয়েছে এশিয়াকে দমন করে। তারপরও প্রাচ্যের মন্দ দিককে ইয়েটস গ্রহণ করেননি।
লেখক-জাহিদ হোসেন
অবসরপ্রাপ্ত কৃষি ব্যাংক কর্মকর্তা